মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতি কি? কারণ, প্রভাব ও সমাধান
আপনার কষ্টার্জিত টাকার মান কেন কমে যাচ্ছে? মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতি কি, এর পেছনের কারণ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে জানুন।
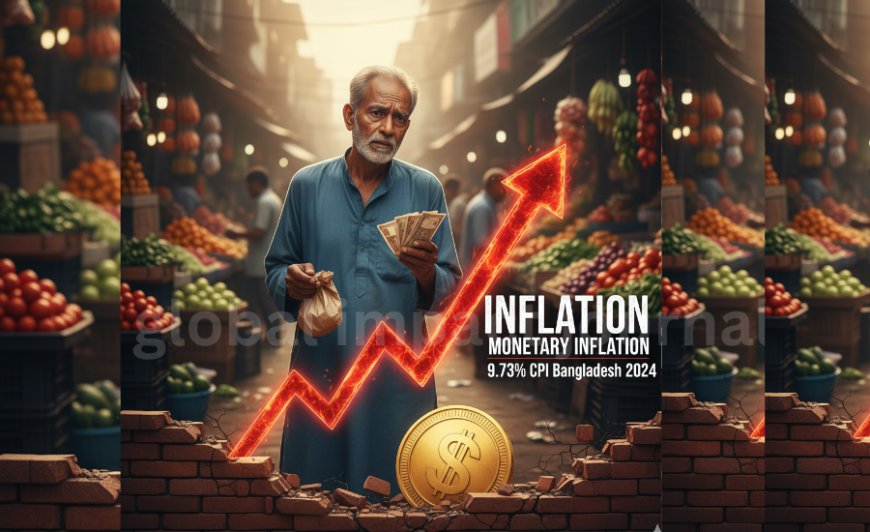
- ভূমিকা
- মূল্যস্ফীতি বনাম মুদ্রাস্ফীতি: অর্থের খেলার সহজ পাঠ
- মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ: চাহিদা এবং খরচের টানাপোড়েন
- বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির উত্থান: নেপথ্যের কারণগুলো কী?
- যেভাবে মাপা হয় মূল্যস্ফীতি: CPI-এর আদ্যোপান্ত
- জনজীবন থেকে অর্থনীতি: মূল্যস্ফীতির বহুমাত্রিক প্রভাব
- নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা: বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের নীতি এবং তার কার্যকারিতা
- ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ: বাংলাদেশ কোন পথে?
- উপসংহার: সমন্বিত পদক্ষেপই স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি
ভূমিকা
ঢাকার কোনো এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কর্তা হয়তো খেয়াল করছেন, মাসের বাজারের বাজেট কিছুতেই আর নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। যে এক হাজার টাকার নোট দিয়ে বছরখানেক আগেও অনায়াসে সপ্তাহের বাজারের বাজার হয়ে যেত, এখন তা দিয়ে তিন দিনের প্রয়োজন মেটানোই কঠিন হয়ে পড়েছে । এই যে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া, এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি এক নীরব অর্থনৈতিক ক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি, যার প্রাতিষ্ঠানিক নাম 'মূল্যস্ফীতি'। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে যে কয়েকটি গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তার মধ্যে মূল্যস্ফীতি এবং এর পেছনের চালিকাশক্তি 'মুদ্রাস্ফীতি' অন্যতম প্রধান । এই দুটি ধারণা সাধারণ মানুষের জীবন থেকে শুরু করে দেশের বৃহৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পর্যন্ত সবকিছুকেই প্রভাবিত করছে।
এই প্রতিবেদনে আমরা মূল্যস্ফীতি ও মুদ্রাস্ফীতির মৌলিক ধারণা, তাদের মধ্যকার কার্যকারণ সম্পর্ক, বাংলাদেশে এর উত্থানের পেছনের কারণ এবং এর বহুমাত্রিক প্রভাব নিয়ে একটি বিশদ ও তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরব। একই সাথে, এই সংকট মোকাবেলায় গৃহীত সরকারি নীতিগুলোর কার্যকারিতা নিয়েও একটি সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করা হবে, যা এই জটিল অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে বুঝতে সাহায্য করবে।
মূল্যস্ফীতি বনাম মুদ্রাস্ফীতি: অর্থের খেলার সহজ পাঠ
অর্থনীতির আলোচনায় 'মূল্যস্ফীতি' এবং 'মুদ্রাস্ফীতি' শব্দ দুটি প্রায়ই একসাথে ব্যবহৃত হলেও এদের অর্থ ও কার্যকারণ সম্পর্ক ভিন্ন। একটি হলো কারণ এবং অন্যটি তার ফল। এই পার্থক্যটি বোঝা বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য অপরিহার্য।
মূল ধারণা: কারণ ও ফল
মুদ্রাস্ফীতি (Monetary Inflation): সহজ ভাষায়, মুদ্রাস্ফীতি হলো একটি দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রা বা টাকার যোগান বা সরবরাহ বেড়ে যাওয়া । যখন কোনো দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা ছাপায় অথবা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ব্যাপক হারে ঋণ প্রদান করে, তখন বাজারে মোট টাকার পরিমাণ বেড়ে যায় । এটিই মুদ্রাস্ফীতির মূল ভিত্তি। অর্থাৎ, পণ্যের উৎপাদনের হারের চেয়ে যদি টাকা ছাপানোর হার বেশি হয়, তবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।
মূল্যস্ফীতি (Price Inflation): অন্যদিকে, মূল্যস্ফীতি হলো পণ্য ও সেবার সাধারণ মূল্যস্তরের ক্রমাগত বৃদ্ধি, যার ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় । এটি হলো সেই পরিস্থিতি যা সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত বাজারে গিয়ে অনুভব করে। যখন একই পরিমাণ টাকা দিয়ে আগের চেয়ে কম পণ্য বা সেবা কেনা যায়, তখন আমরা বলি মূল্যস্ফীতি ঘটেছে ।
কার্যকারণ সম্পর্ক: একটি সরল উদাহরণ
এই দুটি ধারণার মধ্যে সম্পর্কটি একটি সহজ উদাহরণের মাধ্যমে বোঝা যায়। ধরা যাক, একটি ছোট বাজারে মোট ১০০ কেজি চাল আছে এবং সেই চাল কেনার জন্য মানুষের হাতে মোট ১০,০০০ টাকা আছে। এক্ষেত্রে প্রতি কেজি চালের গড় দাম হবে ১০০ টাকা। এখন, যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরও ১০,০০০ টাকা ছাপিয়ে বাজারে ছাড়ে, কিন্তু চালের পরিমাণ ১০০ কেজিই থাকে, তাহলে মানুষের হাতে মোট ২০,০০০ টাকা থাকবে। ফলে, একই পরিমাণ চাল কেনার জন্য মানুষ বেশি টাকা খরচ করতে চাইবে এবং বিক্রেতারাও দাম বাড়িয়ে দেবে। এতে প্রতি কেজি চালের দাম বেড়ে ২০০ টাকা হয়ে যেতে পারে।
এখানে, বাজারে অতিরিক্ত ১০,০০০ টাকা আসাটা হলো মুদ্রাস্ফীতি (টাকার যোগান বৃদ্ধি), এবং এর ফলে চালের দাম কেজিপ্রতি ১০০ টাকা থেকে বেড়ে ২০০ টাকা হওয়াটা হলো মূল্যস্ফীতি (পণ্যের দাম বৃদ্ধি) । সুতরাং, টেকসই মূল্যস্ফীতির পেছনে প্রায় সবসময়ই মুদ্রাস্ফীতি বা অর্থের অতিরিক্ত যোগান একটি বড় কারণ হিসেবে কাজ করে ।
বাংলাদেশের জন পরিসরে এবং গণমাধ্যমে প্রায়শই এই দুটি শব্দকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যা একটি বড় ধারণাগত বিভ্রান্তি তৈরি করে। এই বিভ্রান্তির ফলে সংকটের মূল কারণ (মুদ্রাস্ফীতি বা টাকার যোগান বৃদ্ধি) আড়ালে থেকে যায় এবং মানুষের ক্ষোভ শুধুমাত্র উপসর্গের (মূল্যস্ফীতি বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি) উপর গিয়ে পড়ে। যখন আলোচনা শুধুমাত্র বাজার সিন্ডিকেট বা সরবরাহ ঘাটতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা সরবরাহ নীতি বা সরকারের ঘাটতি বাজেট অর্থায়নের মতো মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে পর্যাপ্ত প্রশ্ন তোলা হয় না। এর ফলে মুদ্রানীতির কার্যকারিতা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে একটি স্বচ্ছ ও গভীর বিতর্ক বাধাগ্রস্ত হয়। এই প্রতিবেদনের অন্যতম লক্ষ্য হলো এই কার্যকারণ সম্পর্কটি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে একটি সঠিক আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।
সম্পর্কিত অন্যান্য ধারণা
- বিস্ফীতি (Deflation): এটি মূল্যস্ফীতির ঠিক বিপরীত অবস্থা, যেখানে পণ্য ও সেবার দাম ক্রমাগত কমতে থাকে। শুনতে ভালো মনে হলেও, ডিফ্লেশন অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। কারণ দাম কমার প্রত্যাশায় মানুষ ভোগ ও বিনিয়োগ পিছিয়ে দেয়, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে স্থবির করে দেয় এবং বেকারত্ব বাড়ায় ।
- মুদ্রার অবমূল্যায়ন (Currency Devaluation): এটি হলো যখন কোনো দেশের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে নিজ দেশের মুদ্রার মান কমিয়ে দেয়। এর মূল উদ্দেশ্য থাকে রপ্তানি বৃদ্ধি করা এবং আমদানি কমানো। যদিও মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে আমদানি পণ্যের দাম বেড়ে গিয়ে মূল্যস্ফীতিকে উস্কে দিতে পারে, এটি মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে ভিন্ন একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত ।
মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ: চাহিদা এবং খরচের টানাপোড়েন
মূল্যস্ফীতি কেন ঘটে, তার ওপর ভিত্তি করে অর্থনীতিবিদরা একে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেন: চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত এবং ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি। বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে এই দুটি প্রকারই সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।
চাহিদা-বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি (Demand-Pull Inflation)
যখন "অল্প কিছু পণ্যের পেছনে অতিরিক্ত অর্থ ধাওয়া করে", তখন এই ধরনের মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়। অর্থাৎ, অর্থনীতিতে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের যে সক্ষমতা রয়েছে, তার চেয়ে যখন সামগ্রিক চাহিদা বেড়ে যায়, তখন বিক্রেতারা দাম বাড়াতে শুরু করে ।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:
- বাড়তি ভোগ: প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণের সহজলভ্যতার কারণে মানুষের হাতে অতিরিক্ত অর্থ এসেছে, যা ভোগব্যয় বাড়িয়েছে ।
- সরকারি ব্যয়: সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে, যার একটি অংশ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অর্থায়ন করা হয়। এই অতিরিক্ত অর্থ বাজারে এসে চাহিদার ওপর চাপ সৃষ্টি করে ।
- প্রণোদনা প্যাকেজ: কোভিড-১৯ মহামারির পর অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে সরকার যে প্রণোদনা প্যাকেজগুলো দিয়েছিল, সেগুলোও বাজারে তারল্য বা টাকার যোগান বাড়িয়ে চাহিদা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখেছে ।
ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত মূল্যস্ফীতি (Cost-Push Inflation)
যখন উৎপাদন উপকরণের খরচ (যেমন কাঁচামাল, জ্বালানি, শ্রমিকের মজুরি) বেড়ে যায়, তখন কোম্পানি গুলো তাদের মুনাফা ঠিক রাখতে পণ্যের দাম বাড়িয়ে দেয়। এটি সরবরাহজনিত (supply-side) মূল্যস্ফীতি ।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:
বাংলাদেশের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।
- আমদানি নির্ভরতা: বাংলাদেশ জ্বালানি তেল, ভোজ্যতেল, শিল্পের কাঁচামালসহ বহু নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য আমদানির ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের দাম বাড়লে তা সরাসরি দেশের ভেতরের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দেয় ।
- টাকার অবমূল্যায়ন: ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমে যাওয়ায় আমদানি করা সব পণ্যের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এটি উৎপাদন খরচের ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করেছে ।
- সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো আন্তর্জাতিক সংকট এবং বন্যা বা বন্যার মতো অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেশের সরবরাহ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। এতে পরিবহন খরচ বাড়ে এবং পণ্যের দামে তার প্রভাব পড়ে ।
মূল্যস্ফীতির দুষ্টচক্র এবং স্থবির প্রবৃদ্ধি (Stagflation)
বাংলাদেশে বর্তমানে একটি জটিল পরিস্থিতি বিরাজ করছে যেখানে চাহিদা-বৃদ্ধি এবং ব্যয়-বৃদ্ধি—উভয় প্রকার মূল্যস্ফীতি একযোগে অর্থনীতিকে আঘাত করছে। এটি এক ধরনের স্থবির প্রবৃদ্ধির (Stagflation) ঝুঁকি তৈরি করেছে, যেখানে উচ্চ মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও শ্লথ হয়ে যায় । পরিস্থিতিটি এমন এক দুষ্টচক্রে পরিণত হয়েছে যেখানে একটি সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে অন্যটি আরও জটিল আকার ধারণ করছে।
উদাহরণস্বরূপ, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বাড়ে (ব্যয়-বৃদ্ধিজনিত ধাক্কা), তখন দেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ে এবং একই সাথে উৎপাদন কমে গিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে, চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন নীতি সুদহার (policy rate) বাড়ায়, তখন ব্যাংক ঋণের খরচও বেড়ে যায়। এর ফলে, যেসকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যেই উচ্চ কাঁচামালের দামে ধুঁকছিল, তাদের জন্য বিনিয়োগ করা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। এতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আরও সংকুচিত হয়। অর্থাৎ, চাহিদা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে গিয়ে প্রবৃদ্ধির গতি আরও কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। এই নীতিগত উভয়সংকটই বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের যাত্রাকে এতটা কঠিন করে তুলেছে।
বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির উত্থান: নেপথ্যের কারণগুলো কী?
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার বিপজ্জনকভাবে বেড়েছে। এর পেছনে বৈশ্বিক এবং অভ্যন্তরীণ—উভয় ধরনের কারণই দায়ী।
বৈশ্বিক কারণসমূহ
- কোভিড-পরবর্তী সরবরাহ সংকট: ২০২০ সালের মহামারির পর বিশ্বব্যাপী চাহিদা হঠাৎ করে বাড়লেও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে সময় নেয়। এর ফলে বিশ্বজুড়ে পণ্য পরিবহন খরচ বাড়ে এবং কাঁচামালের সংকট দেখা দেয়, যা মূল্যস্ফীতিকে উস্কে দেয় ।
- ভূ-রাজনৈতিক সংকট ২০২২ সালে শুরু হওয়া রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য, সার এবং জ্বালানির বাজারে বড় ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে এসব পণ্যের দাম আকাশচুম্বী হয়, যার সরাসরি প্রভাব বাংলাদেশের মতো আমদানিনির্ভর দেশের ওপর পড়ে ।
অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ
- টাকার ব্যাপক অবমূল্যায়ন: ডলারের বিপরীতে টাকার মান দ্রুত কমে যাওয়া সাম্প্রতিক মূল্যস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ। একসময় যে ডলারের দাম ৮৫ টাকার আশেপাশে ছিল, তা এখন প্রায় ১১৭ টাকায় পৌঁছেছে। এর ফলে আমদানি খরচ প্রায় ৩৫-৪০% বেড়ে গেছে, যা দেশের প্রতিটি পণ্যের দামে প্রভাব ফেলছে ।
- সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতি: দীর্ঘ সময় ধরে বাংলাদেশে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশি ছিল । বিশেষ করে, সরকারের বিশাল বাজেট ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে, যা প্রকারান্তরে নতুন টাকা ছাপানোর সামিল। এই অতিরিক্ত অর্থ বাজারে এসে মূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি করেছে ।
অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত কারণ
- বাজার সিন্ডিকেট: চিনি, ডিম, মুরগি, পেঁয়াজের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে শক্তিশালী সিন্ডিকেটের উপস্থিতি একটি বড় সমস্যা। এই চক্রগুলো কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এবং নিজেদের ইচ্ছামতো দাম বাড়িয়ে দেয়, যা সাধারণ ভোক্তাদের ওপর বিশাল চাপ সৃষ্টি করে ।
- অদক্ষ সরবরাহ ব্যবস্থা: দুর্বল অবকাঠামো, অপর্যাপ্ত হিমাগার এবং পরিবহন ব্যবস্থায় একাধিক মধ্যস্বত্বভোগীর উপস্থিতি কারণে কৃষকের পর্যায় থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে কৃষিপণ্যের দাম কয়েকগুণ বেড়ে যায় ।
বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার (%)
বিভিন্ন অর্থবছরের তুলনামূলক চিত্র
| অর্থবছর (Fiscal Year) | সাধারণ মূল্যস্ফীতি (%) | খাদ্য মূল্যস্ফীতি (%) | খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি (%) |
|---|---|---|---|
| ২০২১-২২ | 7.70 | তথ্য উপলব্ধ নয় | তথ্য উপলব্ধ নয় |
| ২০২২-২৩ | 9.02 | তথ্য উপলব্ধ নয় | তথ্য উপলব্ধ নয় |
| ২০২৩-২৪ | 9.73 | তথ্য উপলব্ধ নয় | তথ্য উপলব্ধ নয় |
| ২০২৪-২৫ (আগস্ট) | 8.29 (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) | 7.60 (পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট) | তথ্য উপলব্ধ নয় |
উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS), বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে সংগৃহীত ডেটার ভিত্তিতে সারণিটি তৈরি করা হয়েছে । খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির বিস্তারিত বিভাজন সব বছরের জন্য সহজলভ্য নয়। উপরের সারণি থেকে স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতির হার ২০২১ সালের পর থেকে দ্রুতগতিতে বেড়েছে এবং ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা ৯ শতাংশের উপরে অবস্থান করে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় সতর্ক সংকেত। তবে ২০২৫ সালের আগস্ট মাসে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে ৮.২৯ শতাংশে নেমে এসেছে ।
যেভাবে মাপা হয় মূল্যস্ফীতি: CPI-এর আদ্যোপান্ত
মূল্যস্ফীতি পরিমাপের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, যা ছাড়া অর্থনীতির সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশে এই কাজটি করে থাকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)।
ভোক্তা মূল্য সূচক (Consumer Price Index - CPI)
মূল্যস্ফীতি পরিমাপের সবচেয়ে প্রচলিত এবং স্বীকৃত পদ্ধতি হলো ভোক্তা মূল্য সূচক বা CPI । CPI মূলত একটি নির্দিষ্ট বাজার ঝুড়িতে (market basket) থাকা বিভিন্ন পণ্য ও সেবার গড় মূল্যের পরিবর্তনকে পরিমাপ করে। এই ঝুড়িতে এমন সব পণ্য ও সেবা থাকে যা একটি দেশের সাধারণ পরিবারগুলো তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করে।
বাজার ঝুড়ি ও ভিত্তি বছর:
- BBS সম্প্রতি মূল্যস্ফীতি পরিমাপের জন্য ভিত্তি বছর (base year) পরিবর্তন করে ২০০৫-০৬ থেকে ২০২১-২২-এ উন্নীত করেছে। এর ফলে বর্তমান ভোগ প্রবণতার একটি সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব হচ্ছে ।
- এই নতুন ঝুড়িতে গ্রামীণ ও শহর উভয় এলাকার জন্য মোট ৩৮৩টি পণ্য এবং ৭৪৯টি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার (varieties) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আবাসন, যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবাসহ মোট ১২টি প্রধান ক্যাটাগরি ।
তথ্য সংগ্রহ ও গণনা:
- BBS সারা দেশ থেকে মোট ১৫৪টি বাজার (৯০টি শহর এবং ৬৪টি গ্রামীণ) থেকে নিয়মিতভাবে এসব পণ্যের দামের তথ্য সংগ্রহ করে ।
- এই সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে CPI সূচক তৈরি করা হয়। কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মূল্যস্ফীতির হার হলো পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় CPI সূচকের শতকরা পরিবর্তন। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৫ সালের আগস্ট মাসের মূল্যস্ফীতির হার বের করার জন্য ২০২৪ সালের আগস্ট মাসের CPI-এর সাথে তুলনা করা হয় ।
সরকারি পরিসংখ্যান বনাম জনমানুষের অভিজ্ঞতা
যদিও CPI মূল্যস্ফীতি পরিমাপের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, প্রায়শই সরকারিভাবে প্রকাশিত মূল্যস্ফীতির হারের সাথে সাধারণ মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার একটি বড় পার্থক্য দেখা যায়। এর পেছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে:
- গড় হিসাবের সীমাবদ্ধতা: CPI একটি গড় হিসাব। কিন্তু নিম্ন আয়ের পরিবারের খরচের একটি বড় অংশই (প্রায় ৭০% বা তার বেশি) যায় খাদ্যপণ্য কিনতে। তাই যখন খাদ্যপণ্যের দাম সাধারণ মূল্যস্ফীতির হারের চেয়ে অনেক বেশি বাড়ে, তখন এই পরিবারগুলো যে চাপ অনুভব করে, তা সরকারি পরিসংখ্যানে পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় না ।
- ভোগের ভিন্নতা: CPI ঝুড়িতে থাকা সব পণ্য সব শ্রেণির মানুষ সমানভাবে ভোগ করে না। তাই নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বাড়লে, যেসব পরিবার ওই পণ্য বেশি ব্যবহার করে, তাদের জন্য ব্যক্তিগত মূল্যস্ফীতির হার সরকারি গড়ের চেয়ে অনেক বেশি হয়।
- তথ্যের যথার্থতা: অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, BBS যে তথ্য সংগ্রহ করে, তা বাজারের প্রকৃত অবস্থাকে, বিশেষ করে সিন্ডিকেটের কারণে সৃষ্ট আকস্মিক মূল্য বৃদ্ধিকে, সবসময় সঠিকভাবে তুলে ধরতে পারে না ।
এই ফারাকের কারণে সরকারি পরিসংখ্যানের প্রতি এক ধরনের জন-অনাস্থা তৈরি হয়। একটি বিশেষজ্ঞ-স্তরের বিশ্লেষণে তাই শুধুমাত্র সরকারি পদ্ধতি বর্ণনা করাই যথেষ্ট নয়, বরং এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা এবং এর ফলে সৃষ্ট জন-অভিজ্ঞতার পার্থক্যকে স্বীকার করে নেওয়াটাও জরুরি।
জনজীবন থেকে অর্থনীতি: মূল্যস্ফীতির বহুমাত্রিক প্রভাব
উচ্চ মূল্যস্ফীতি শুধুমাত্র একটি অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান নয়; এটি দেশের প্রতিটি নাগরিক এবং অর্থনীতির প্রতিটি খাতের ওপর গভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।
নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারের ওপর প্রভাব
মূল্যস্ফীতিকে প্রায়শই "সবচেয়ে নিষ্ঠুর কর" (cruelest tax) হিসেবে অভিহিত করা হয়, কারণ এটি সমাজের দরিদ্র এবং নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি আঘাত হানে।
- ক্রয়ক্ষমতা ক্ষয়: যাদের আয় নির্দিষ্ট বা মূল্যস্ফীতির হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ে না, তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। এর ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে ।
- খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা: বাংলাদেশের নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোর আয়ের সিংহভাগ খাদ্যের পেছনে ব্যয় হয়। খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণে এই পরিবারগুলো আমিষ (মাছ, মাংস, ডিম) এবং এমনকি চাল-ডালের মতো মৌলিক খাবারের ভোগ কমাতে বাধ্য হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৯৭% পর্যন্ত পরিবার তাদের আমিষ গ্রহণ কমিয়েছে ।
- বাধ্যতামূলক সমন্বয়: খাদ্যের খরচ মেটাতে গিয়ে পরিবারগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পোশাকের মতো অন্যান্য জরুরি খাতে ব্যয় সংকোচন করতে বাধ্য হয়। অনেকে সন্তানদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়ার কথাও ভাবেন ।
- ঋণ ও সঞ্চয় ক্ষয়: দৈনন্দিন খরচ মেটাতে না পেরে বহু পরিবার ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ছে অথবা তাদের সারাজীবনের সঞ্চয় ভেঙে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৭৪% পরিবারকে ঋণ করতে হয়েছে এবং ৫৬% পরিবারের সঞ্চয়ের সুযোগ নষ্ট হয়েছে ।
সঞ্চয়কারী এবং প্রকৃত সুদের হার
মূল্যস্ফীতি সঞ্চয়কারীদের জন্য একটি নীরব ঘাতক। এর প্রভাব বোঝার জন্য 'প্রকৃত সুদের হার' (Real Interest Rate) ধারণাটি বোঝা জরুরি।
প্রকৃত সুদের হার = নামিক সুদের হার (Nominal Interest Rate) - মূল্যস্ফীতির হার (Inflation Rate)
এটিই হলো আপনার সঞ্চয়ের ওপর প্রকৃত আয়। বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে মূল্যস্ফীতির হার ব্যাংক আমানত এবং সঞ্চয়পত্রের সুদের হারের চেয়ে বেশি ছিল, যার ফলে প্রকৃত সুদের হার ছিল ঋণাত্মক । এর অর্থ হলো, ব্যাংকে টাকা রেখেও মানুষ প্রতি বছর তাদের ক্রয়ক্ষমতা হারাচ্ছে।
ব্যাংক আমানতের উপর প্রকৃত আয়
মূল্যস্ফীতি বনাম আমানতের সুদের হার
| বছর | গড় মূল্যস্ফীতি (%) | গড় ব্যাংক আমানত হার (%) | প্রকৃত আয় (%) |
|---|---|---|---|
| ২০২৩ | 9.50 | 6.52 | -2.98 |
| ২০২৪ | 10.47 | 8.52 | -1.95 |
উৎস: বিশ্বব্যাংক এবং ycharts থেকে সংগৃহীত।
এই সারণিটি স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে একজন সঞ্চয়কারী ব্যাংকে টাকা রেখে নামমাত্র সুদ পেলেও, উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে তার সঞ্চয়ের প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা আসলে কমে গেছে। এই পরিস্থিতি মানুষকে আনুষ্ঠানিক সঞ্চয়ে নিরুৎসাহিত করে এবং দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় ।
ব্যবসা ও বিনিয়োগের ওপর প্রভাব
উচ্চ এবং অস্থিতিশীল মূল্যস্ফীতি দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।
- খরচ বৃদ্ধি ও অনিশ্চয়তা: জ্বালানি, কাঁচামাল এবং পরিবহন খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME), উৎপাদন খরচ ব্যাপক হারে বেড়েছে। এটি তাদের পরিকল্পনা এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি করে ।
- মুনাফা হ্রাস: অনেক প্রতিষ্ঠান, বিশেষত এসএমই, বর্ধিত খরচ পুরোপুরি ভোক্তার ওপর চাপাতে পারে না, কারণ তাতে বিক্রি কমে যাওয়ার ভয় থাকে। এর ফলে তাদের মুনাফার হার (profit margin) সংকুচিত হয়ে যায় ।
- বিনিয়োগে বাধা: উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করে। এটি অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ (যেমন নতুন কারখানা স্থাপন) এবং প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) উভয়কেই নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে । মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন সুদের হার বাড়ানো হয়, তখন ঋণ নিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণ করাও ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, যা বিনিয়োগকে আরও বাধাগ্রস্ত করে ।
নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা: বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের নীতি এবং তার কার্যকারিতা
উচ্চ মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা ধরনের নীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক রয়েছে।
মুদ্রানীতির পদক্ষেপ (বাংলাদেশ ব্যাংক)
বাংলাদেশ ব্যাংক সম্প্রতি মুদ্রানীতির কাঠামোতে একটি বড় পরিবর্তন এনেছে। তারা মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পুরোনো পদ্ধতি থেকে সরে এসে সুদহারকে প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার নীতি গ্রহণ করেছে ।
- নীতি সুদহার বৃদ্ধি: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক তার নীতি সুদহার (রেপো রেট) দফায় দফায় বাড়িয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর জন্য তহবিল সংগ্রহের খরচ বাড়িয়ে দেওয়া, যাতে তারা ঋণ বিতরণে নিরুৎসাহিত হয় এবং বাজারে টাকার প্রবাহ কমে । ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথমার্ধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সতর্ক সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বজায় রেখেছে এবং নীতি সুদহার ৮.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রেখেছে ।
- রিজার্ভের প্রয়োজনীয়তা: ব্যাংকগুলোকে তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাধ্যতামূলকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হয় (CRR ও SLR)। এই হার পরিবর্তন করেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ দেওয়ার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ।
রাজস্ব নীতির পদক্ষেপ (সরকার)
- ভর্তুকি ও সামাজিক সুরক্ষা: সরকার খোলা বাজারে বিক্রি (OMS) এবং ট্রেডিং কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশের (TCB) মাধ্যমে কম দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি করে দরিদ্র মানুষকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে ।
- বাজার তদারকি: সিন্ডিকেট এবং মজুতদারদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও করা হয় ।
- বাজেট লক্ষ্যমাত্রা: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সরকার মূল্যস্ফীতির হার ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ।
কার্যকারিতার সমালোচনামূলক মূল্যায়ন
বিশেষজ্ঞদের মতে, এই নীতিগুলো মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আশানুরূপ ফল দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পেছনে কয়েকটি গভীর কারণ রয়েছে:
- বিলম্বিত পদক্ষেপ: অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, বাংলাদেশ ব্যাংক সুদহারের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা (৯% ঋণের সুদহারের সীমা) সরাতে অনেক দেরি করেছে। যখন মূল্যস্ফীতি বাড়তে শুরু করেছিল, তখন এই কৃত্রিম সুদহারের কারণে বাজারে সস্তা টাকার প্রবাহ বন্ধ করা যায়নি, যা সংকটকে আরও গভীর করেছে ।
- নীতিগত স্ববিরোধিতা: মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে কাজ করেছে নীতিগত স্ববিরোধিতা। একদিকে বাংলাদেশ ব্যাংক সুদহার বাড়িয়ে মুদ্রা সরবরাহ কমানোর (সংকোচনমূলক নীতি) চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সরকার তার বাজেট ঘাটতি মেটাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেই বিপুল পরিমাণ ঋণ নিচ্ছে, যা বাজারে নতুন টাকা ছাড়ার সামিল (সম্প্রসারণমূলক নীতি) । এছাড়া, তারল্য সংকটে থাকা কিছু ব্যাংককে সহায়তা করতে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নতুন টাকা ছাপাতে হয়েছে, যা তার মূল্যস্ফীতি-বিরোধী অবস্থানের সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক ।
- দুর্বল সঞ্চালন ব্যবস্থা (Weak Transmission Mechanism): উন্নত দেশগুলোর মতো বাংলাদেশে মুদ্রানীতির সঞ্চালন ব্যবস্থা ততটা শক্তিশালী নয়। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার বাড়ালেও তার প্রভাব ব্যাংক ঋণের সুদহার এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে পড়তে অনেক সময় লাগে এবং এর কার্যকারিতাও কম ।
এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে একটি গভীর প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার সংকট। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতার অভাব, রাজনৈতিক এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর চাপের কাছে নতি স্বীকার করার প্রবণতা এবং নীতিগত স্ববিরোধিতা—এই সবকিছু মিলিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ওপর সাধারণ মানুষ ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা কমে গেছে । যখন মানুষ বিশ্বাস করে না যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সত্যিই আন্তরিক, তখন তাদের মধ্যে মূল্যস্ফীতি বাড়ার প্রত্যাশা তৈরি হয়। এই প্রত্যাশাই মূল্যস্ফীতিকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাজকে আরও কঠিন করে দেয়। সুতরাং, সমস্যাটি শুধু ভুল নীতি গ্রহণের নয়, বরং নীতির কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনেরও।
ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ: বাংলাদেশ কোন পথে?
মূল্যস্ফীতির সংকট বাংলাদেশে নতুন নয়। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং ভবিষ্যতের পূর্বাভাস বিশ্লেষণ করে সঠিক পথ নির্ধারণ করা অত্যন্ত জরুরি।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট
- ১৯৭১-পরবর্তী অতি-মূল্যস্ফীতি: স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ এক ভয়াবহ অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছিল। ধ্বংসপ্রাপ্ত অবকাঠামো এবং ভেঙে পড়া সরবরাহ ব্যবস্থার কারণে ১৯৭২-৭৪ সালে দেশে মূল্যস্ফীতির হার ৩০০% থেকে ৪০০% পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল । এটি একটি চরম উদাহরণ যে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার বিপর্যয় কতটা ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।
- বৈশ্বিক উদাহরণ: জার্মানির ভাইমার প্রজাতন্ত্রে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লাগামহীন টাকা ছাপানোর ফলে সৃষ্ট হাইপারইনফ্লেশন (অতি-মূল্যস্ফীতি) এবং ১৯৭০-এর দশকে তেল সংকটের কারণে পশ্চিমা বিশ্বে সৃষ্ট স্ট্যাগফ্লেশন—এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। প্রথমত, মুদ্রা সরবরাহের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালে তার পরিণতি কী হতে পারে এবং দ্বিতীয়ত, সরবরাহজনিত ধাক্কা কীভাবে একটি অর্থনীতিকে একযোগে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্বের দিকে ঠেলে দিতে পারে । বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই দুটি উদাহরণই প্রাসঙ্গিক।
ভবিষ্যতের পূর্বাভাস
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং অর্থনৈতিক মডেল বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ মূল্যস্ফীতি নিয়ে পূর্বাভাস দিয়েছে। এই পূর্বাভাসগুলো একটি মিশ্র চিত্র তুলে ধরে, তবে সাধারণ প্রবণতা হলো ধীরে ধীরে হ্রাসের দিকে।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB): এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এপ্রিল ২০২৫-এর পূর্বাভাস অনুযায়ী, ২০২৫ অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ১০.২% থাকতে পারে, তবে ২০২৬ অর্থবছরে তা কমে ৮.০% এ নেমে আসার সম্ভাবনা রয়েছে । এই হ্রাসের পেছনে অনুকূল আবহাওয়া, বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমা এবং কঠোর মুদ্রানীতি ও রাজস্ব নীতি ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে ।
- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF): আইএমএফ-এর এপ্রিল ২০২৫-এর পূর্বাভাসে বলা হয়েছে যে, ২০২৫ সালে গড় মূল্যস্ফীতি প্রায় ১০ শতাংশ থাকবে এবং এরপর তা ধীরে ধীরে কমে ৫ শতাংশের কাছাকাছি আসবে ।
- অন্যান্য ইকোনোমেট্রিক মডেল: কিছু ইকোনোমেট্রিক মডেল দীর্ঘমেয়াদী পূর্বাভাসে আরও আশাবাদী চিত্র দেখিয়েছে। তাদের মতে, ২০২৬ সালে মূল্যস্ফীতি ৪.০০ শতাংশ এবং ২০২৭ সালে ৫.০০ শতাংশের কাছাকাছি থাকতে পারে ।
তবে এই পূর্বাভাসের পেছনে বেশ কিছু ঝুঁকিও রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম আবার বাড়লে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হলে অথবা অভ্যন্তরীণ নীতিগত দুর্বলতা অব্যাহত থাকলে মূল্যস্ফীতির চাপ কমানো কঠিন হবে ।
উপসংহার: সমন্বিত পদক্ষেপই স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি
উপরের বিশদ বিশ্লেষণ থেকে এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি কোনো একক কারণে সৃষ্ট সমস্যা নয়। এটি বৈশ্বিক সংকট, দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ নীতিগত দুর্বলতা এবং গভীর কাঠামোগত সমস্যার এক জটিল মিশ্রণ। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নেমে এসেছে অসহনীয় চাপ, সঞ্চয় হারিয়ে যাচ্ছে এবং দেশের বিনিয়োগ পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
শুধুমাত্র সুদহারের মতো একটি বা দুটি হাতিয়ার দিয়ে এই বহুমাত্রিক সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এর জন্য একটি সমন্বিত এবং সামগ্রিক পদক্ষেপ প্রয়োজন, যেখানে মুদ্রানীতি এবং রাজস্ব নীতির মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় থাকবে। একটি বিশ্বাসযোগ্য ও টেকসই সমাধানের জন্য নিম্নলিখিত চারটি স্তম্ভের ওপর ভিত্তি করে একটি কৌশল প্রণয়ন করা অপরিহার্য:
- ধারাবাহিক ও বিশ্বাসযোগ্য মুদ্রানীতি: একটি স্বাধীন এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক, যার একমাত্র লক্ষ্য হবে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং টাকার স্থিতিশীলতা রক্ষা করা।
- বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার প্রবণতা কমিয়ে আনা এবং কর ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সরকারের আয় বৃদ্ধি করা।
- কাঠামোগত সংস্কার: বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ, সরবরাহ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা।
- লক্ষ্যভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা: মূল্যস্ফীতির কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, যাতে তারা এই কঠিন সময় পার করতে পারে। এই সমন্বিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা না গেলে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসা বাংলাদেশের জন্য কঠিন হবে। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির পথে ফিরে যাওয়ার জন্য সাহসী এবং দূরদর্শী নীতি গ্রহণ এখন সময়ের দাবি।
বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ)
প্রশ্ন ১: মূল্যস্ফীতি এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে মূল পার্থক্য কি?
উত্তর: মুদ্রাস্ফীতি হলো অর্থনীতিতে টাকার যোগান বেড়ে যাওয়া (কারণ), আর মূল্যস্ফীতি হলো জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়া (তার ফল)। সহজ কথায়, অতিরিক্ত টাকা ছাপালে মুদ্রাস্ফীতি হয়, যার পরিণতিতে মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়।
প্রশ্ন ২: বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি বাড়ার প্রধান কারণ কী?
উত্তর: এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি ও খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি, ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন, সরকারের অতিরিক্ত ব্যাংক ঋণ গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণ বাজারে সিন্ডিকেটের মতো বিষয়গুলো এর জন্য প্রধানত দায়ী।
প্রশ্ন ৩: মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে?
উত্তর: এটি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে দেয়, ফলে একই আয় দিয়ে আগের চেয়ে কম জিনিস কেনা যায়। এটি সঞ্চয় ক্ষয় করে এবং বিশেষ করে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারকে খাদ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসার মতো মৌলিক চাহিদা মেটাতে হিমশিম খেতে হয়।
প্রশ্ন ৪: সরকার কি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে?
উত্তর: হ্যাঁ, বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রা সরবরাহ কমাতে সুদের হার বাড়িয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সরকার মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেছে। এছাড়া সরকার খোলা বাজারে পণ্য বিক্রি (OMS) এবং ভর্তুকির মতো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে এসব পদক্ষেপের কার্যকারিতা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে, কারণ একই সাথে সরকারের ব্যাংক ঋণ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।






















